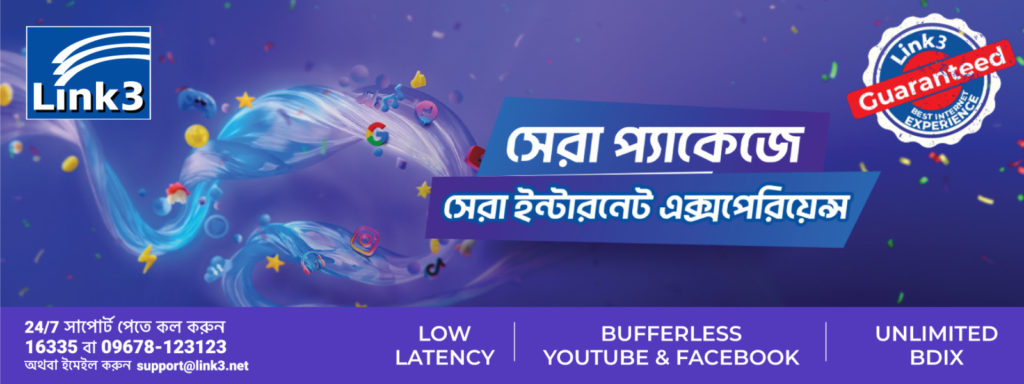অনলাইন ডেস্ক
অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও বাজারে আস্থা ফিরিয়ে আনতে ব্যাংক খাতকে সংস্কার করার যে পদক্ষেপ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হাতে নিয়েছে তা এখন দেশের আর্থিক ভবিষ্যতের মোড় ঘোরানোর অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। সম্প্রতি আলোচনায় এসেছে পাঁচটি ইসলামী ব্যাংককে একীভূত করার উদ্যোগ।
সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ মহল বলছে, এটি ব্যাংক খাতের অনিয়ম ও অনিশ্চয়তা কাটাতে সহায়ক হতে পারে।
কিন্তু অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞদের বড় অংশ বলছেন, “দুর্বল ব্যাংককে দুর্বল ব্যাংকের সঙ্গে জোড়া লাগালে শক্তি নয়, বরং সমস্যা বহুগুণে বাড়বে।”
অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি ব্যাংক ব্যবস্থা। এখানে জনগণের আমানত, শিল্পকারখানার ঋণ, বাণিজ্য ও রেমিট্যান্সের প্রবাহ সবকিছুই ঘুরে। তাই বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার বা যে কোনো স্থিতিশীল সরকারকে প্রথমেই তিনটি বড় ক্ষেত্র ধরে কাজ করতে হবে। আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি ও ঋণ কেলেঙ্কারি প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা ও তদারকি ব্যবস্থার শৃঙ্খলাবদ্ধ পুনর্গঠন।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকারের উচিত এখনই বাংলাদেশ ব্যাংককে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করে স্বতন্ত্র ও কঠোর তদারকি ক্ষমতা দেওয়া। কোনো ব্যাংককে বাঁচাতে “রাজনৈতিক অনুগ্রহ বা প্রভাবশালী মালিকের ছাড়” যেন না দেওয়া হয় এই নীতি বাস্তবায়নই অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রথম ধাপ।
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন একজন গভর্নর বলেছেন, “একীভূতকরণ তখনই সুফল দেয়, যখন দুর্বল ব্যাংককে শক্তিশালী ব্যাংকের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে, সমস্যাগ্রস্ত ইসলামী ব্যাংকগুলোর বেশিরভাগই নিজে দুর্বল। তাই সেগুলো একত্র করলে স্থিতিশীলতা নয়, বরং ‘সমষ্টিগত দুর্বলতা’ তৈরি হবে।”
বর্তমানে দেশে মোট ১০টি ইসলামী ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে পাঁচটি ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে নেমে গেছে। খেলাপি ঋণ, অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক প্রভাব ও অস্বচ্ছ বিনিয়োগের কারণে এই ব্যাংকগুলোর আমানতকারীদের আস্থা ক্রমেই কমে যাচ্ছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, সরকারের আলোচনায় থাকা একীভূতকরণের তালিকায় রয়েছে, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, এক্সিম ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক।
এদের মধ্যে প্রথম তিনটি ব্যাংকের বড় অংশের আমানত ও ঋণ খাতে বিপুল অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্ত প্রতিবেদনেও দেখা গেছে, কিছু ব্যাংক আমানতকারীর অর্থ ব্যবহার করেছে অনুমোদনবিহীন খাতে; আবার কোথাও কোথাও একই জামানত দেখিয়ে একাধিক ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে।
একীভূতকরণের তত্ত্ব বলে, দুটি বা একাধিক প্রতিষ্ঠান একীভূত হলে তাদের ব্যয় কমে, ব্যবস্থাপনা খরচ কমে যায়, এবং কার্যক্রমের দক্ষতা বাড়ে। একই সঙ্গে ব্যাংকগুলোর মূলধন বাড়ে এবং গ্রাহকের আস্থা কিছুটা ফিরে আসে।
তবে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমস্যাটি উল্টো দিকেও যেতে পারে। কারণ, এই ব্যাংকগুলোর অধিকাংশই একই ধরনের আর্থিক সংকটে ভুগছে।
একজন বিশিষ্ট ব্যাংকার নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, “পাঁচটা দুর্বল ব্যাংক একত্র করলে হবে পাঁচগুণ দুর্বলতা। এখানে একীভূতকরণ নয়, প্রয়োজন কঠোর পুনর্গঠন ও জবাবদিহিতা।”
একীভূতকরণের আগে প্রত্যেক ব্যাংকের ব্যালান্স শিট, দায়-সম্পদ এবং বাস্তব আমানতের হিসাব স্বচ্ছভাবে নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। অনেক ব্যাংক তথাকথিত “ইসলামী বিনিয়োগ” বা মুরাবাহা-মুদারাবা চুক্তির আড়ালে সাধারণ ঋণের মতোই অস্বচ্ছ কার্যক্রম চালিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে এসব ব্যাংকের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থান নির্ধারণ করা ছাড়া মার্জার হলে তা হতে পারে “সংগঠিত আর্থিক বিপর্যয়।”
সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন জনগণের আমাদের টাকা কি নিরাপদ? যদি এই ব্যাংকগুলোর আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হয়, তাহলে আমানতকারীরা ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে গিয়ে ভয়াবহ সংকটে পড়বেন।
অর্থনীতিবিদরা বলেন, “ব্যাংক একীভূতকরণ মানে সমস্যা ঢেকে রাখা নয়; বরং সমস্যার প্রকৃতি বদলে দেওয়া। যদি সরকার বাস্তবসম্মত পুনর্গঠন পরিকল্পনা না দেয়, তবে গ্রাহকের টাকা ফেরত পাওয়া নিশ্চিত করা কঠিন হবে।”
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, একীভূত ব্যাংকগুলোর জন্য সরকারকে একটি ‘ডিপোজিট গ্যারান্টি স্কিম’ চালু করতে হবে যাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত আমানত সরকারের গ্যারান্টির আওতায় থাকে। পাশাপাশি প্রতিটি ব্যাংকে স্বাধীন অডিট ফার্ম দিয়ে সম্পূর্ণ আর্থিক যাচাই-বাছাই করতে হবে, যাতে জনগণ বুঝতে পারে তাদের টাকা কোথায় আছে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ব্যাংক খাতের বর্তমান সংকট মোকাবেলায় সরকারকে বেশকিছু গুরত্বপূর্ণ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে হবে।
তাদের মতে, ব্যাংক খাতে নামধারী ও ছদ্মমালিকদের বের করে প্রকৃত মালিকানার নথি উন্মুক্ত করতে হবে। খেলাপি ঋণের পুনর্গঠন নীতিমালা আরও কঠোর করতে হবে। রাজনৈতিক প্রভাবিত ঋণ পুনঃতফসিলের সুযোগ বন্ধ করতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ ব্যাংককে আর্থিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করতে হবে, যাতে তারা কোনো রাজনৈতিক নির্দেশ নয়, অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে প্রাধান্য দেয়। একীভূত হওয়া ব্যাংকগুলোর আর্থিক অবস্থা ‘স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক অডিট’ দ্বারা যাচাই করতে হবে। ব্যাংক ব্যর্থ হলে যাতে গ্রাহক ক্ষতিপূরণ পান তার জন্য আমানত সুরক্ষা তহবিল কার্যকর করতে হবে। বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে অনলাইন জালিয়াতি ও অনুমোদনহীন লেনদেন প্রতিরোধে বিশেষ সেল গঠন করতে হবে।
বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করেন, একীভূতকরণের চেয়ে আরও কার্যকর উপায় হতে পারে “ব্যবস্থাপনা পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে পুনর্গঠন” অর্থাৎ, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পুনর্গঠন করে দক্ষ ব্যাংকারদের হাতে দায়িত্ব দেওয়া। এর মাধ্যমে ব্যর্থ ব্যাংকগুলোকেও ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।
অর্থনীতিবিদ ড. মোস্তাফিজুর রহমানের ভাষায়, “আমাদের দেশে ব্যাংক ব্যর্থ হয় ব্যবস্থাপনাগত দুর্নীতি, অনিয়ম ও প্রভাবশালীদের অবাধ ক্ষমতার কারণে। এগুলো ঠিক না করলে আপনি ব্যাংক মার্জার করুন বা নাম বদলান ফলাফল একই থাকবে।”
অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সরকারের সামনে এখন দুটি রাস্তা খোলা। একদিকে সংস্কার, অন্যদিকে আপোষ। কিন্তু আপোষেল পথ বেছে নিলে ব্যাংক খাত শুধু আরও গভীর অন্ধকারে ডুবে যাবে। একীভূতকরণ হতে পারে একটি কাঠামোগত উদ্যোগ, কিন্তু সেটি হবে ফলপ্রসূ কেবল তখনই যখন সরকার রাজনৈতিক প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠে আর্থিক জবাবদিহিতা ও ব্যাংক তদারকির নতুন সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করবে।
কারণ, অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার আসল মূলধন শুধু টাকা নয় আস্থা। আর সেই আস্থা ফিরিয়ে আনাই আজ সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।রুহেল হাশেমী