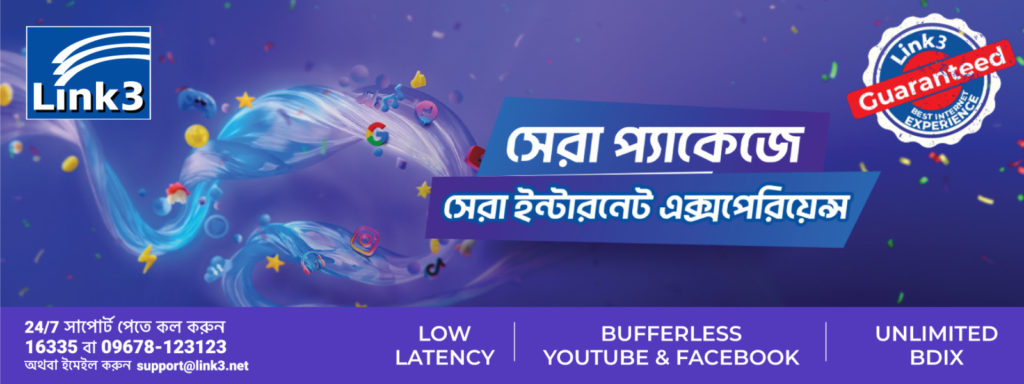অনলাইন ডেস্ক
প্রতিদিনের রুটিনে আমরা যতই অচেতন হই না কেন, সকালের নাস্তা থেকে রাতের ভোজন ও খাবার এখন অনেক মানুষের জন্য অচেনা এক ঝুঁকি নিয়ে আসে। বাজারে ঝকঝকে, টাটকা দেখানো মাছ, টাটকা সবজি, চকচকে ফল আর এসবের আড়ালে লুকিয়ে থাকে ফরমালিন, অনুপ্রবেশকারী কীটনাশক, আর সুযোগলুপ্ত প্রক্রিয়াজাত কেমিক্যাল। এই বস্তুনিষ্ঠ কিন্তু অদৃশ্য ‘বিষ’ শরীরে জমে যায় ধীরে ধীরে কিডনি, লিভার, হরমোনাল ব্যালান্স, স্মৃতিশক্তি ও দীর্ঘ মেয়াদি ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। দেশে খাদ্য নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনি খাতেও যে আপডেট চলছে, তবু বাস্তব জীবনে সাধারণ মানুষ প্রতিদিন অনিশ্চয়তার সামনে দাঁড়ায়। সরকার, খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও নাগরিক, তিনপক্ষের মিলিত পদক্ষেপ ছাড়া এ ‘নীরব যুদ্ধ’ জয় করা যাবে না।
এই বিষ সমস্যার প্রকৃতি বিস্তৃত: একটি ধারাবাহিকতার মতো কৃষকের মাঠে উচ্চ মাত্রার কীটনাশক ও হারের প্রলোভন, বাজারে খুচরা বিক্রেতার অল্প মুনাফার জন্য খাবার রং-চকচকে করে ঢোকানো এবং ভ্যান, বাজার-মধ্যস্থ শুরুর লজিস্টিক্যাল ঝুঁকিতে দেড়-দু’তলায় সংরক্ষণে রাসায়নিক প্রয়োগ। এর সঙ্গে যোগ করুণ খাবার ত্বরান্বিত করার জন্য অনানুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহার করা হয় ক্যালসিয়াম কার্বাইড (সুতা পাকা করতে), অথবা মাছ ও ফল সংরক্ষণে ফরমালিন। সমস্যা যদি একদিকে ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার অসতর্কতা হয়, অন্যদিকে সেটি সামাজিক-নৈতিক এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার দৃষ্টান্তও বটে।
কীভাবে এই রণকৌশল আমাদের খাদ্যসংক্রান্ত রোগ বাড়ায়? দীর্ঘকালীন গবেষণা ও পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে ফরমালিন (ফরমালডিহাইড) ও অনেক প্রকার কীটনাশক শরীরে জমে ধীরে ধীরে অঙ্গপ্রতঙ্গের নষ্টসৃষ্টি করে আর এবিশেষত কিডনি ও লিভারের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে এবং কিছু কেমিক্যাল জৈবনিক পুনর্জীবিত হতে গিয়ে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। এই কারণে ‘আজ না, কাল না’ বলেই কেউ কেউ এ কন্টামিনেটেড খাদ্য খেয়ে ক immediate immediate অসুস্থ হয়ে পড়ে না উপসর্গগুলো সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সামনে আসে। তাই যাদের বিষাক্ত খাদ্য গ্রহণ দীর্ঘদিন চলেছে, তাদের রোগ বহুবিধ ও জটিলতর হয় আর এ বিষয়ে রোগীদের ইতিহাস যতই অনিশ্চিত হোক, জনস্বাস্থ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ নজরদারি অত্যাবশ্যক।
তাই এখন প্রশ্ন আসে এ সমস্যার উৎস কোথায়? এবং কীভাবে আমরা প্রতিদিনকার আর্ন্তজাতিক/স্থানীয় বাস্তবে নিজের পরিবারকে নিরাপদ রাখব?
হতাশার আগে জেনে নেওয়া যাক সমস্যার বড় কারণগুলো:
কৃষি পদ্ধতিতে অতিরিক্ত ও অনুপযুক্ত কীটনাশক প্রয়োগ: কৃষকের কাছে কীটনাশক ব্যবহারের সহজ সমাধান ও উচ্চ ফলন চাহিদা প্রবলের সঙ্গে বেড়েছে। স্টোরেজ বা রোগ প্রতিরোধে অনুমোদিত এবং অনানুমোদিত উভয় কেমিক্যাল ব্যবহার হচ্ছে, কোনো কোনো সময় বিক্রেতা বা পাইকারি বাজারে বিক্রি বাড়াতে অতিরিক্ত কেমিক্যাল প্রয়োগের লোভে পড়ে। গবেষণা ও সার্ভে রিপোর্টগুলো দেখায় শস্য উৎপাদনের সঙ্গে কীটনাশকের ব্যবহার বেড়েছে এবং তার ফলে ফল-সবজিতে রেসিডিউ রয়েছে।
বাজারে অনিয়ম, দুর্বল তদারকি ও অপর্যাপ্ত গবেষণাগার সুবিধা: বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অনেক উন্নতি হলেও মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত নজরদারি, দ্রুত পরীক্ষার সক্ষমতা ও জরুরি আইন প্রয়োগ এখনও সীমিত। খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ (BFSA) আইনি কাঠামো আপডেট করার চেষ্টা করলেও, কর্মসূচি প্রয়োগ ও মনিটরিংয়ের ঘাটতি থেকে অনিয়ম অব্যাহত থাকে।
ভোক্তাদের সীমিত সচেতনতা ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা: ক্ষুদ্র ক্রেতা প্রায়ই সস্তা ও টাটকা দেখানো পণ্যের দিকে ঝুঁকে যায় আর তার মানে সবসময় নিরাপদ নয়। আর অনেক ক্ষেত্রেই বিক্রেতার পক্ষ থেকে ‘ফার্মার’ না, বরং কৃষক ও মধ্যস্বত্ত্বভোগীর মধ্যে তথ্য বিচ্ছিন্ন থাকে ক্রেতা জানেনা ঠিক কীভাবে উত্পাদিত হয়েছে।
এখন আসি সবচেয়ে জরুরি অংশে ব্যক্তিগত ও স্মার্ট প্রতিরোধ:
বাজার থেকে কেনার সময় সতর্কতা ও চিহ্নিত পদানুসরণ: সবজি ও ফল কিনতে গেলে ছোট কৃষক-কেন্দ্রিক মেলা বা প্রত্যক্ষ-বিক্রেতা থেকে যেটুকু সম্ভব কিনুন যারা উৎপাদকদের সাথে সরাসরি কাজ করে, অথচ নিশ্চিত হওয়ার মতো কোনো পথ না থাকলেও কম না।
মাছ কিনে গৃহে আনার আগে তাজা দেখালেই কৌতূহল বাঁচবেন না, যদি মাছের গন্ধ অস্বাভাবিক না থাকে, কিন্তু অতিরিক্ত কঠোর টেকসই-দেহ থাকে, অনেকে সেটা ফরমালিন মনে করতে পারেন আর তেমন সন্দেহ হলে বিক্রেতাকে প্রশ্ন করুন এবং প্রয়োজনে লাইসেন্স চেয়ে নিন। কিছু বাজারে পোর্টেবল টেস্ট কিট দিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়, যা স্থানীয় প্রশাসন কখনো কখনো র্যাপিড টেস্ট চালায়, দেখা গেলেও সহযোগিতা দাবি করুন।
বাড়িতে সচেতনভাবে পরিষ্কার করা কীটা কার্যকর, কীটা নয়: বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে সাধারণ ধোয়া, ভাজার প্রক্রিয়া এবং খোসা ছেঁড়া অনেক ক্ষেত্রে পেস্টিসাইড রেসিডিউ কমাতে কার্যকর। তবে সব ধরনের কেমিক্যাল পুরোপুরি আর দূর করা যায় না, কিছু কীটনাশক ফসলের ভিতরে প্রবেশ করে যায়। যার ফলে শুধুই ধোয়া দিয়ে সব রেসিডিউ দূর হয় না। গবেষণা অনুযায়ী লিফি ভেজিটেবলগুলোতে ধোয়া, সোয়াল-সচেতন ধোয়া, এবং ব্লাঞ্চিং/বোলিং/স্টার-ফ্রাইয়ের মাধ্যমে রেসিডিউ ২০%-৭০% পর্যন্ত কমেছে। আবার কিছূ ক্ষেত্রে ১০০% পর্যন্তও কমে গেছে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে (যেমন ব্লাঞ্চিং)।
অন্যদিকে, ফলের ক্ষেত্রে পিলিং (খোসা ছাড়ানো) সবচেয়ে কার্যকর: অনেক পেস্টিসাইড বাহ্যিক দিকেই থাকে। খোসা ছাড়ালে বেশিরভাগ রেসিডিউ কমে যায়। তবে খেয়াল রাখবেন খোসা ছেঁড়ে খাওয়ার ফলে ভিটামিন-ফাইবারও কমে। তাই এটা দীর্ঘমেয়াদে সব খাদ্যই খোসা ছাড়া খাবেন এমন মানে নয়।
রান্নার সময় উপায়: কড়া রান্না/ফোঁড়ানো, বুশিং, বেটে রান্না কিছু কীটনাশক গরমে ভাঙে, ফলে রান্নার মাধ্যমে কিছুটা হ্রাস পায়। গবেষণা বলছে, ব্লাঞ্চিং বা উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করলে নির্দিষ্ট রেসিডিউ কমে। তবে সব কেমিক্যালই তাপমাত্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না। তাই রান্নার কৌশলই মূল সমাধান নয় এটা এক অন্তর্বর্তী রোধ মাত্র।
সংরক্ষণ ও প্যাকেজিংয়ের সন্ধান: স্টোর করা খাবারে সাবধানতা প্রস্তুত খাবার বেশি সময় রেখে না খাওয়া, মৃতদেহ-সদৃশ গন্ধ বা অস্বাভাবিক রং দেখলেই তৎক্ষণাত ফেলে দিন বা জব্দ করুন।
স্থানীয় পরিবেশ ও বাজারে পরীক্ষা চালাতে অনুরোধ জানাবেন কমিউনিটি পর্যায়ে র্যাপিড টেস্ট কিট এনে নিয়মিত স্ট্রিং টেস্ট করলে উক্ত বাজারে বিক্রেতাদের সতর্কতা বাড়ে।
কিন্তু ব্যক্তিগত সতর্কতা যথেষ্ট নয়, এখানে কাঠামোগত সংস্কার জরুরি। নীচে প্রস্তাবিত নীতিনির্দেশ:
শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: BFSA এর আইনি সংস্কারের মধ্যে অগ্রগতি হলেও মাঠ পর্যায়ে ল্যাব, মনিটরিং ইউনিট ও দ্রুত র্যাপিড টেস্টিং ইউনিট বাড়াতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা আইনকে বাস্তবিক ক্ষমতা দিয়ে প্রয়োগে আনতে হবে। বাজার-স্তর থেকে র্যামপ্যানিং অ্যাডালটেশন বন্ধ করতে সক্ষম নিয়ম এবং কঠোর জরিমানা বসাতে হবে।
কৃষকদের জন্য নিরাপদ চাষাবাদের বাস্তব সহায়তা ও প্রণোদনা: জমিতে সঠিক কীটনাশক ব্যবহার, বিকল্প জৈবীয় পদ্ধতি (ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট—IPM), রোটেশন কৌশল এবং সার্টিফাইড বীজ বা জৈব সার ব্যবহার আর এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা দরকার। মুনাফার স্বল্পতায় যে কৃষক অনাকাঙ্খিতভাবে অপ-approved কেমিক্যাল নেয়, তাদের জন্য বিকল্প ও সহায়তা মেকানিজম রাখতে হবে।
বাজারে র্যাম্প-আপ: এনএমপি টেস্টিং ও ট্রেসাবিলিটি সিস্টেম: আর্ন্তজাতিকভাবে প্রমাণিত ‘মার্চিং’ ট্রেসাবিলিটি সিস্টেম চাই। কোন পণ্য কোথা থেকে এসেছে, কীভাবে সংগ্রহ ও পরিবহন হয়েছে এই তথ্য থাকলে অনিয়ম ধরতেও সুবিধা হবে। বিক্রেতাদের লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক অবস্থানে আনুন এবং নিয়মিত অডিট করান।
গ্রাহক সচেতনতা ও সমাজিক জবাবদিহিতা বৃদ্ধি: টিভি, রেডিও, সামাজিক প্ল্যাটফর্ম সব মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বার্তা দিতে হবে। গ্রামীণ স্তরে যে ‘অজানা প্রচলন’ চলছে তার বিরুদ্ধে শিক্ষা ও সচেতনতা অভিযান খুব জরুরি। স্থানীয় ভোক্তা অধিকার সংস্থাগুলোকে শক্তিশালী করে তোলা দরকার যাতে তারা বাজার পর্যায়ে র্যাপিড চেক চালাতে পারে।
দ্রুত আইন প্রয়োগ সকলে আইনের কাছে সমান: যারা খাদ্যে ফরমালিন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও অন্যান্য হুমকিসৃষ্ট কেমিক্যাল ব্যবহার করে, তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা দ্রুত ও দৃশ্যমানভাবে গ্রহণ করতে হবে। আইনি শাস্তির কার্যকর উপস্থিতি বাজারে ভীতি সৃষ্টি করবে। এটাই দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের এক বাস্তব উপায়।
এই লড়াই জয় করা সম্ভব। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন একটি সচেতন সমাজ, জবাবদিহিমুখী প্রশাসন এবং কৃষি-অর্থনৈতিক নীতিতে প্রকৃত সংস্কার। ব্যক্তিগত তৎপরতাও দরকার। আর আপনি যখন থেকে সবজি/ফল/মাছ কিনবেন, তখন একটু বাড়তি সতর্কতা, ধোয়া ও পরিমার্জনের কিছু উপায় অবলম্বন করলে, দৈনিক আপনার পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা কিছুটা বেড়ে যাবে। একই সঙ্গে, আমাদের সংবাদপত্র, আদালত, শিল্পী, সামাজিক সংগঠন মিলিয়ে যদি এটি নিয়ে দৃঢ়তা দেখাই, তাহলে কেবল আজকের নয়, আগামীর প্রজন্মও বিষমুক্ত খাদ্য পাবে।
আজ আপনার টেবিলে উঠা খাবার যদি সত্যিই আপনার পরিবারের জন্য মৃত্যুহীন, সুস্থতার নিশ্চয়তা হয়। তার জন্য প্রয়োজন সবার জোরালো দাবি: মাঠ থেকে প্লেট পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা, শক্তিশালী তদারকি, কৃষককেন্দ্রিক সহায়তা ও আইনের কঠোর প্রয়োগ। অন্যথায়, প্রতিদিনই আমরা আমাদের শরীরকে একটু একটু করে বিক্রি করে দিচ্ছি। আর জানিনা কখন আমাদের সমাজের জেনারেশন-ওয়াইস স্বাস্থ্য একটি অনিয়ন্ত্রিত ক্ষতিতে পরিণত হবে।
হাশেম রেজা
লেখক: কলামিস্ট ও সাংবাদিক/জেএইচআর