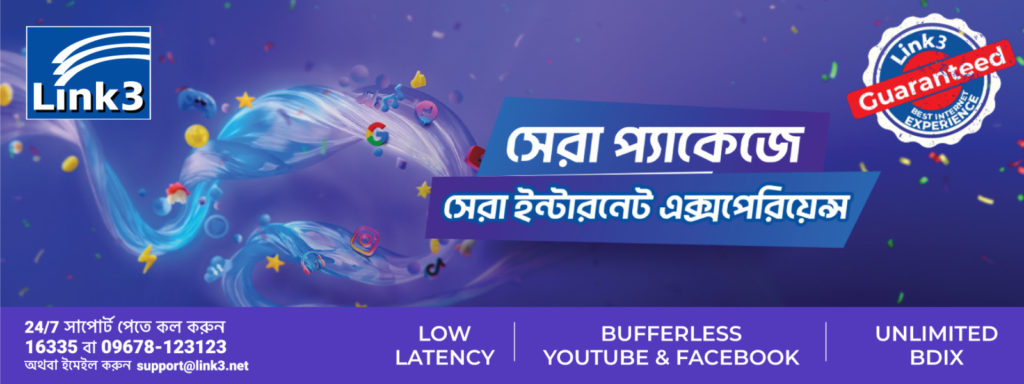জাতীয় ডেস্ক
দেশের ভবনগুলোর প্রায় ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে, যা বড় ধরনের ভূমিকম্পের সময় অত্যন্ত গুরুতর ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি করছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, ভবন নির্মাণে কাঠামোগত দুর্বলতা ও নির্মাণ কোড অনুসরণ না করার কারণে ভূমিকম্পের সঙ্গে অগ্নিকাণ্ড বা অন্যান্য বিপর্যয়ও সংঘটিত হতে পারে।
সাম্প্রতিক সময়ে ভূমিকম্পের দম বন্ধ করা সতর্কতা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। ২০২৫ সালের ২১ নভেম্বর সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে দেশে ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এর পাশাপাশি পরপর কয়েকটি ছোট ভূমিকম্পও অনুভূত হয়েছে। রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে এই ভূমিকম্পের ফলে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ভূমিকম্প চলাকালীন আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের জন্য নির্দেশনা দিয়েছে।
ভূমিকম্পসহ বড় ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য ফায়ার সার্ভিস ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। চলতি বছরের মে মাসে অপারেশনাল বিভাগকে রাজধানীর মিরপুরে স্থানান্তর করা হয়েছে। ঢাকা শহরে দ্রুত উদ্ধার সেবা প্রদানের জন্য ৬০ সদস্যের একটি স্পেশাল কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। দেশের অন্যান্য বিভাগীয় শহরেও ২০ সদস্যের একটি করে স্পেশাল টিম প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এছাড়া, ডিরেক্টর ট্রেনিং ও ডেভেলপমেন্ট বিভাগকে পূর্বাচলে স্থানান্তর করা হচ্ছে।
ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল বলেন, বড় ধরনের ভূমিকম্পের সময় ফায়ার সার্ভিস একা তা মোকাবিলা করতে পারবে না। ভূমিকম্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারি সেবা যেমন পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, সওয়ারেজ লাইনও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলে ভবন ধ্বস ও মানুষ হতাহত হওয়ার ঝুঁকি আরও বৃদ্ধি পাবে। এজন্য সমস্ত সরকারি ও অ-সরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রস্তুতি অপরিহার্য।
রাজউকের ২০১৮ থেকে ২০২২ সালের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, যদি ঢাকায় ৭.৫ বা তারও বেশি মাত্রার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, তবে প্রায় ছয় লাখ ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং দেড় থেকে দুই লাখ মানুষ মারা যেতে পারে। এতে বিপুল সংখ্যক ভবন ধ্বসে পড়া এবং রাস্তা, বৈদ্যুতিক ও গ্যাস লাইনের ক্ষতি সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ কার্যক্রমকে কঠিন করবে।
ভূমিকম্প-প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ভলান্টিয়ার এবং সাধারণ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫৮ হাজার প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ার তৈরি করা হয়েছে, যারা জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা প্রদান করবে। এছাড়া উদ্ধার কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বিভিন্ন স্টেশনে, পূর্বাচলে এবং মিরপুরে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে।
ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক লে. কর্নেল এম এ আজাদ আনোয়ার বলেন, ভূমিকম্পের আগেই কোনো পূর্বনির্দেশনা পাওয়া যায় না। এজন্য দুই স্তরের প্রস্তুতি জরুরি: একটি হলো ভবন নির্মাণ ও রেট্রোফিটিং, যাতে ভবন ভূমিকম্প সহনীয় হয়; দ্বিতীয়ত হলো মানুষের মধ্যে আতঙ্ক কমানো ও সচেতনতা বৃদ্ধি। হাইরাইজ ভবনে থাকা মানুষদের উচিত প্যানিক না করে ভবনের শক্তিশালী অংশে আশ্রয় নেওয়া এবং মাথা ঢেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
এছাড়া জরুরি অবস্থার জন্য শুকনা খাবার, পানি, টর্চলাইট, ব্যাটারি, রেডিওসহ ‘ইমার্জেন্সি প্যাক’ প্রস্তুত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। হাইরাইজ ভবনের নিচ তলায় থাকলে নিরাপদ খোলা স্থানে সরাসরি যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে।
ভূমিকম্পের ঝুঁকি বাড়ার পেছনে বাংলাদেশের ভূ-ভৌগোলিক অবস্থানও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় প্লেট, ইউরেশিয়ান প্লেট ও বার্মিজ মাইক্রোপ্লেটের সংযোগস্থলের নিকটে অবস্থান বাংলাদেশের ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা করে তুলেছে। অপরিকল্পিত অবকাঠামোর কারণে ঢাকার মতো ঘনবসতিপূর্ণ শহরে বড় ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। ২০০৯ সালে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি ও জাইকার যৌথ জরিপে বলা হয়েছে, ঢাকায় ৭ বা তার বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হলে ৭২ হাজার ভবন ধ্বসে পড়বে এবং ১ লাখ ৩৫ হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
ভূমিকম্প গবেষক ও সাবেক উপাচার্য সৈয়দ হুমায়ুন আখতার উল্লেখ করেছেন, মাত্র ১ শতাংশ ভবন বিধ্বস্ত হলে ঢাকায় প্রায় ৬০০০ ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং অন্তত ৩ লাখ মানুষের জীবন ঝুঁকিতে পড়বে। ভূমিকম্প-পরবর্তী উদ্ধার ও সেবা কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে আরও বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটতে পারে।